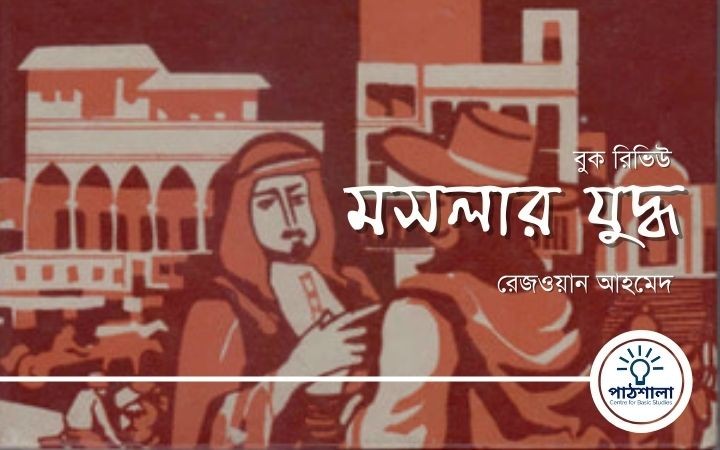
মসলার যুদ্ধ
আমরা সকলে জানি প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে ভারতবর্ষে পা রাখা লোকটির নাম ভাস্কো দা গামা। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে তিনি এ অঞ্চলে আসেন জলপথে। কিন্তু তার আসার আগের সার্বিক পরিস্থিতির একটা বিবরণ ভূমিকার মতো করে জানা আছে আমাদের? যদি জানা না থেকে থাকে, সত্যেন সেনের বন্দিদশায় রচিত ক্ষুদ্রায়তন বই 'মসলার যুদ্ধ' আমাদেরই জন্য।
ভাস্কো দা গামার অভিযান ছিল দশ মাস বারো দিন দৈর্ঘ্যের। তিনি যে পর্তুগাল থেকে অভিযান করেছিলেন তার জন্য তিনি প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয় রাজ্য যথাক্রমে ভেনিস-জেনোয়ার মধ্যকার ব্যাবসায়িক প্রতিযোগিতা এবং পরে মিলিন্দির রাজা এবং তাঁর নিযুক্ত একজন ভারতীয় নাবিকের সহযোগিতার কাছে ঋণী। বলাবাহুল্য, পুরো প্রক্রিয়াটাই খ্রিস্টদের ক্রুসেডের মনোভাব অবলম্বনে সমাধা হয়েছিলো। মূলত ভাস্কো দা গামাকে যে এদিকে আসবার জলপথ আবিস্কারের কৃতিত্ব দিই আমরা, এটা ভুল।
একদিকে কালিকট বন্দরের রাজা জামোরিন ভাস্কো দা গামাকে বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন শুল্ক মার্জনার অসঙ্গত আবদার মেনে নিয়ে, অন্যদিকে ভারতভূমির ব্যাপারে দা গামার এই সফরপূর্ব ভুল অনুসন্ধানের কিছু ফিরিস্তি মিলল।
দ্বিতীয় অভিযান আরো পরিকল্পিত, সুসজ্জিত এবং সুচিন্তিত ছিল পর্তুগিজদের। তারা শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণ ব্যবসার ধার ধারেনি। ফলে হাঙ্গামাপ্রসূত উপায়ে মসলার যুদ্ধের সূচনা ঘটেছিল। পর্তুগালের তৎকালীন রাজা ডোম ম্যানুয়েল আফ্রো-এশীয় বাণিজ্য ও নৌ-চলাচলের মৌখিক প্রভুত্ব ঘোষণা করে বসলেন তখন। রোমান পোপের পর্যন্ত সমর্থন এক্ষেত্রে ছিল। পর্তুগিজদের দেখাদেখি ডাচ, ফরাসি, ইংরেজরাও এদিকে এল। সে প্রসঙ্গে পরে আসি।
দ্বিতীয় অভিযানে ভাস্কো দা গামা অধিনায়ক হিসেবে ওই মৌখিক প্রভুত্বের ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করে গেলেন। পোপের সমর্থন থাকায় তার জলদস্যুসুলভ আচরণও বৈধতা পেল। তাতে কপাল এবং প্রাণ—দুইই পুড়ল সমসাময়িক আরবীয় হজ-যাত্রীদের। একেবারে নির্বিচার বিবেকহীনতায়। আন্তর্জাতিক আইন নামেই আন্তর্জাতিকতার তকমা পেয়েছিল সে সময়।
এতকিছুর পরও প্রথম প্রথম কিছুই প্রায় করেননি কালিকট রাজা জামোরিন। শেষমেশ যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো তাঁর, নগরবণিকদের সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধ লড়বেন ভাস্কো দা গামার বিরুদ্ধে। অকল্পনীয়ভাবে সেই অসম লড়াইয়ে খোজা আম্বরের আন্তরিকতা আর সেনাপতি কাশিমের দৃঢ়তায় পিছু হটলেন ভাস্কো দা গামা। অথচ যুদ্ধের কথা কালিকটিদের মাথায় কখনো আসেনি এর আগে।
দা গামা নিরুদ্দেশ হবার পর লোপো সোর্স্-এর আচমকা আক্রমণের মুখে যুদ্ধে আবার ক্ষতিগ্রস্ত হলো কালিকটের জাহাজগুলো। কামানের কাছে হার মেনে মিশরের সাহায্য চাইলেন কালিকটরাজ। পেলেন প্রাচীন সেনাপতি মীর হুসেনকে। এ পর্যায়ে মিশর কালিকটকে কামানও সরবরাহ করে। চাওল নামক স্থানে সংঘটিত হয় সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। আবার পিছু হটে পর্তুগিজ বহর।
মুখোমুখি তৃতীয় যুদ্ধে অবশ্য পর্তুগিজরা শেষ হাসি হাসে। মিশরকেও পরে দিতে হয় চড়া মূল্য।
যুদ্ধে জিতলেও কালিকট অধিকার করা সম্ভব হয়নি পর্তুগালের পক্ষে। শেষমেশ ১৫৯৯ সালে দুপক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। তবে মসলার বাণিজ্যে পর্তুগাল ঠিকই কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। এজন্য তারা এফনসো অ্যালবুকার্কের কাছে ঋণী নিঃসন্দেহে।
কালিকটকে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে যথাযথ সহযোগিতা করার কোনো উদ্যোগ যে দেখা যায়নি, তার পেছনে রয়েছে মুসলমানবিদ্বেষী মনোভাব। পর্তুগিজদেরও ত ওটাই অস্ত্র। ক্রুসেডের মনোভাবটা স্পষ্ট ত ওখানেই।
পর্তুগিজরা গোয়া দখল করে সহজেই। এরপর তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলো, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার দিকে মনোযোগ দেয় মসলার প্রয়োজনে। ততদিনে এদিকের ওপর থেকে চিনা প্রভাব নিঃশেষিত হয়েছে। এদিকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের দুর্বলতাটাকে তারা কাজে লাগায়।
ইন্দোনেশিয়া দখলের জন্য তারা প্ৰথমে মালাক্কা অধিকার করে। একপর্যায়ে জাভার সমুদ্রে কর্তৃত্ব কায়েম করে বসে পর্তুগিজরা।
পর্তুগিজদের এই অন্যায় সমুদ্রশাসন রুখে দিতে এক হয়েছিল চারপক্ষ—তুরস্কের সুলতান, কালিকট ও ক্যাম্বের রাজা এবং মিশরের সুলতান। তবে এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।
দেখা যায়, সর্বত্রই পর্তুগিজরা শুধুমাত্র আরব মুসলিম হটানোর নীতি অবলম্বন করে এবং কালিকট ছাড়া সর্বত্রই সফল হয়। অন্য সর্বত্র হিন্দুদের কাছে এরা প্রশ্রয় পায় ওই বিদ্বেষপ্রসূত কারণেই। দেশীয় বণিকরাও এ ব্যাপারে পর্তুগিজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সে সময়।
মার্টিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রভাবে মসলা বাণিজ্যে রাশ পড়ে পর্তুগিজদের। এ সুযোগে ডাচ বণিকরা ইন্দোনেশিয়ায় ঢুকে পড়ে। ফলে গড়ে ওঠে ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পর্তুগিজদের তাড়াতে ডাচরা বদ্ধপরিকর ছিল। ডাচদের কাছে পরাজিত হতে হতে পর্তুগিজরা গোয়ায় আশ্রয় নিল।
এরপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রয়োগ করে ডাচরা স্থানীয় লবঙ্গ চাষীদের চাষ নিষিদ্ধ করে, জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে কফির বাগান গড়ে চাষীদের নিজেদের বাগানের কুলিতে পরিণত করল। নজিরবিহীন।
ডাচদের ব্যবসা দেখে ইংরেজ বণিকরা একচেটিয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় এলেও ডাচদের সাথে পেরে না উঠে রণেভঙ্গ দিতে হয়েছে তাদের।
মসলার যুদ্ধ ক্রুসেডপরবর্তী প্রভাবে প্রচুর নিরপরাধ জীবন কেড়ে নেয়। হরণ করে অনেক দেশের স্বাধীনতা। শেষমেশ সাধারণ চাষীদের ডাচ-গোলামী করবার আখ্যান রক্তাক্ত মসলার যুদ্ধ। আজ আমরা যখন-তখন একটুখানি ঝালেঝোলে সুস্বাদু খাবারের খোঁজ করি হেঁসেলে, মসলার যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস খুঁজে দেখতে আমাদের সে আগ্রহ আর সময় কতটুকু?
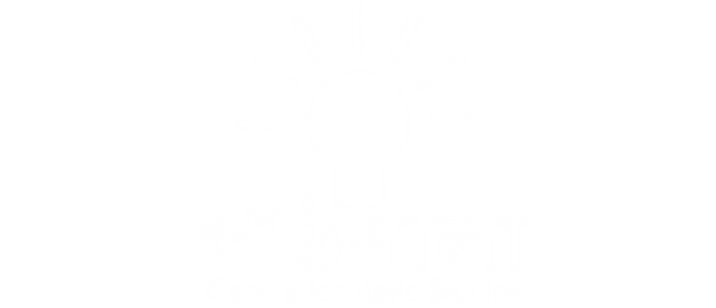
আপনার মন্তব্য লিখুন