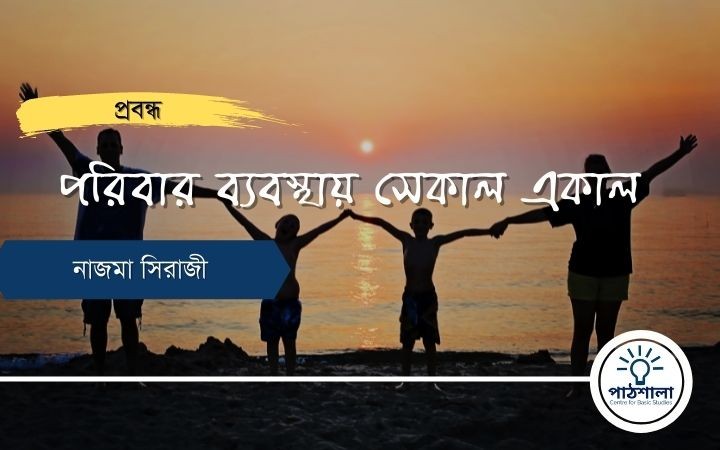
পরিবার ব্যবস্থায় সেকাল একাল
সামাজিক ভিত্তি হিসাবে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা র দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এক একটি পরিবার। আমাদের সবচেয়ে শান্তির জায়গা,নির্ভরতার জায়গা হচ্ছে পরিবার। সারাদিন আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, পরিবারের মানুষগুলোর টানে, সম্পর্কের টানে দিনশেষে ঘরে ফিরি।
সময়ের পালাবদলে কতকিছু যে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার সেই হারিয়ে যাওয়া তালিকায় স্হান করে নিয়েছে আমাদের অত্যন্ত গর্বের, আমাদের ঐতিহ্যের ধারক যৌথ পরিবারগুলো। আমাদের যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে সেখানে স্হান করে নিয়েছে এককপরিবার।
একসময় গ্রাম ও শহর দুই জায়গায়ই যৌথ পরিবারের বেশ কদর ছিল। যত বড় পরিবার তত বেশি প্রভাব, তত বেশি ক্ষমতা। "একের বোঝা দশের লাঠি " এপ্রবাদকে প্রাধান্য দিতেন। যার যত ছেলে -মেয়ে, যার যত বড় গোষ্ঠী তার তত প্রভাব- প্রতিপত্তি,ক্ষমতা। সমাজে চৌধুরী বাড়ি, খন্দকার বাড়ি, শিকদার বাড়ি, খান বাড়ি এরকম কতনামে বড় বড় গোষ্ঠী ছিল। সমাজে এ পরিবারগুলোর একটা আলাদা মর্যাদা ও ছিল। সে যুগে বাবা-মা তাদের সন্তানদের বিয়ে -শাদীর চিন্তা করলে বড় পরিবারে আত্নীয়তার করার স্বপ্ন দেখতেন।
বড় পরিবারগুলোয় আভিজাত্যপূর্ণ বড় বড় বাড়ি, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ঘরভর্তি চাকর-বাকর দেখা যেতো। আর গ্রামের কথা যদি বলি, কত জমি -জিরাত, সান বাঁধানো পুকুর, গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, কত বড় বড় কাচারি ঘর।
বাবা ছেলেরা বা ভাইয়েরা ভাইয়েরা মিলে পারিবারিক ব্যবসা সামলাতেন। সাত আট ভাই কি সুন্দর বিয়ে শাদী করে সবার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে দিব্বি ঘর-সংসার করতেন। ছেলেরা যতই বড় হোক না কেন, বাড়ির কর্তা বাবাই ছিলেন।
মা-বাবার প্রতি ছেলে-মেয়েদের, এমনকি বাড়ির বউদের কি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সমীহ! বাড়ির বউরা শ্বশুর -শ্বাশুড়ীর মুখে মুখে কথা দূরের ব্যাপার চোখ তুলে পর্যন্ত কথা বলতেন না।
পরিবারের সকলের প্রতি সকলের ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। জায়ে জায়ে ছিল কি সখ্য কি মিল! বাড়ির কাজ সবাই ভাগাভাগি করে শেষ করতেন। খাবারের সময় বাড়ির পুরুষরা আগে খেতে বসতেন, তারপর ছেলে-মেয়েরা শেষে বাড়ির বউরা। কে মাছের মাথা খেলো, কে পেটি খেলো এগুলো নিয়ে কখনও অভিযোগ ছিল না।
ছেলে-মেয়ে বড় করা বা লেখাপড়ার ব্যাপারেও বাবা-মার আলাদা কোনো নজর দিতে হতো না। যৌথ পরিবারের ছেলেমেয়েরা কোনো জিনিস শুধু আমার নিজের এব্যাপারগুলো ভাবার সুযোগই পেতেন না। একক বলে কিছু নেই, সব জিনিস সবার সমান এই মতাদর্শেই বড় হতেন। আনন্দটা যেমন সবাই ভাগাভাগি করে উপভোগ করতেন, তেমনি দুঃখ কষ্টগুলোও সবাই সবার মাঝে ভাগ করে নিতেন বা নেয়ার চেষ্টা করতেন।
সকালে মসজিদে গিয়ে সবাই আরবি পড়তেন। তারপর বাড়িতে এসে লজিং মাষ্টারের কাছে স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পড়াশোনা। সেকালে মুটামুটি অবস্থাসম্পূর্ণ গ্রাম কিংবা শহর প্রতিটা গৃহস্থবাড়িতেই একজন লজিং মাষ্টার রাখা হতো। তিনি দুবেলা করে বাড়ির ছেলেমেয়েদের বাংলা, ইংরেজি, অংক শিখাতেন। পড়া শেষে সবাই নিজ নিজ গোসল সেরে নাস্তা করে স্কুলে চলে যেতেন। এভাবেই একদিন স্কুল শেষে কলেজ, কলেজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে নিজেদের বাবা-মার তথা পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করতেন।
একালে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবার প্রাধান্য পেয়েছে। এখন আর কেউ শ্বশুর -শ্বাশুড়ি, ননদ,দেবর, ভাসুর, ডজন ডজন মানুষ নিয়ে থাকতে রাজি না। বিয়ে শাদীর বেলায়ও এযুগের বাবা-মায়ের পছন্দের তালিকায় উঠে এসেছে ছোট পরিবার।
এযুগের মেয়েরাও বিয়ের আগেই স্বামীকে নিয়ে নিজের একটা আলাদা সংসার হবে, সে সংসারে শুধু মাত্র তারই কর্তৃত্ব থাকবে, তার পছন্দের জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হবে, এমনটাই স্বপ্ন দেখতে থাকেন। বড় বাড়ির চেয়ে তারা বহুতল ভবনের কোনো নির্জন ফ্ল্যাটে একক সংসার সাজাতে পছন্দ করেন। বাবা-মার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য, মানবিকতাবোধ, সৌজন্যতাবোধগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে।
সে যুগে ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে না থাকলে বাবা-মায়ের মন ভরতো না। অবস্থাসম্পূর্ণ পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাগাতেন। এটাই ছিল তাদের ঐতিহ্য ও আভিজাত্যর প্রকাশ। বাইরে চাকুরী তেমন পছন্দ ছিল না।
দিন বদলের হাওয়ায় এযুগের দম্পতিরা একটা দুইটা বেশি সন্তান নিতে আগ্রহী নন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে জীবন -যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজনই যখন কর্মজীবি তখন একটা দুইটার বেশি সন্তান নেয়ার সময়ই বা কোথায়। আবার বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক পরিবারে ও একজন দুইজনের বেশি সন্তান দেখা যায় না।
এযুগে পরিবার প্রথাগুলো ভেঙে যাওয়ায় সন্তানরা মানুষ হচ্ছে কোনো ডে-কেয়ার সেন্টারে, না হলে কাজের লোকের কাছে।
সে যুগে বাবা-মা তাদের সন্তানদের চোখে হারাতেন। আর এযুগের বাবা-মা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতে চিন্তা করে পড়ার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন সাত -সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। এ-যুগের সন্তানরা বাবা-মার শরীরের গন্ধ চিনার আগেই আলাদা হয়ে যাচ্ছেন।
বিয়ে-শাদির ব্যাপারে যদি বলি তাহলে, সে যুগে বাবা-মার পছন্দেই বেশির ভাগ বিয়ে হতো। তখনকার দিনে রুপের চেয়ে গুনের কদর, বংশের, পারিবারিক ঐতিহ্যের কদর ছিল বেশি।
আর এ যুগে রুপের কদরের পাশাপাশি পাত্রপাত্রীর বাবার কয়টা বাড়ি আছে, কয়টা গাড়ি আছে, পাত্রের উপরি ইনকাম আছে কিনা (হোক না সেটা অসৎপথে) তাতে অসুবিধা নেই। এগুলো হলো বর্তমান সময়ে পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতার মাপকাঠি। তার সাথে আরও যেদিকটা চোখে পড়ে তাহলো এযুগের পাত্রপাত্রী নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এখানে বাবা-মার পছন্দ অপছন্দের কোনো মূল্য নেই।
শহরের অভিজাত পরিবারগুলোর সেই আভিজাত্যের নিদর্শন, সেই গাছপালা ঘেরা দুতলা, তিনতলা বাড়ি গুলো আজকাল খুব একটা দেখা যায় না। এখানেও পরিবর্তনের ছোঁয়ায় পুরোনো ধাঁচের বাড়িগুলোর জায়গায় স্হান করে নিয়েছে বিশাল বিশাল অট্টালিকাসম বহুতল ভবন। যত ফ্ল্যাট তত টাকা। টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ পরিবারকে সময় দিচ্ছে কম। সে যুগের পারিবারিক আমেজ এযুগের পরিবারগুলোর মধ্যে নেই বল্লেই চলে।
খাবার-দাবারেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। আগে সকালের নাস্তায় শোভা পেত পরোটা, লুচি, তরকারি,মাংস,পায়েস, হালুয়া,বিভিন্নপদের মিষ্টি। আর বর্তমানে খাবারের টেবিলে স্থান করে নিয়েছে - মাখন দিয়ে ডিম পোচ, টোস্ট, ফল আর গ্রীন টি।
দুপুরে সাদা ভাত, ছোট মাছের চড়চ্চরি রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারী, সরর্ষে ইলিশ, বেগুন ভাজা, বড় মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট, দেশি মুরগীর পাতলা ঝোল, আরো কত কী?
আর এখন দুপুরের ভাতের সাথে দুই কিংবা তিনটা আইটেম। আবার কিছু কিছু পরিবার বাইরে থেকে অর্ডার করা খাবারেই কাজ সারছেন।
অনেক পরিবারে আবার বাঙালী খাবারের পরিবর্তে তাদের পছন্দের তালিকায় উঠে এসেছে ইন্ডিয়ান, থাই,চাইনিজ,কোরিয়ান ডিসগুলো। মায়ের হাতের খাবারের জন্য সন্তানের যে আকুতি, এখনকার দিনের সন্তানদের মধ্যে সেই আকুতির বড় অভাব।
সে যুগের ছেলে-মেয়েরা শহর কিংবা গ্রামে খোলা মাঠে খেলাধূলা করে আনন্দময় শৈশব পার করতেন। দাঁড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, বৌয়াচি,সাতচারা ছিল ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলা। আর এ যুগে বিনোদনের মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল, ট্যাব,কম্পিউটার বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম।
সেযুগে চাচাতো-মামাতো, ফুফাতো, খালাতো ভাই -বোনদের সাথে কি মিল ছিল! সুযোগ পেলেই সব আত্নীয় পরিজন একসাথে হয়ে আনন্দে মেতে উঠতো।আর এখন পরিবারগুলো এতোটাই ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে যান যে, একজনের বিপদে অন্যজনকে কাছে পাওয়াও যেন সৌভাগ্যের ব্যাপার।
এই যান্ত্রিকতার যুগে মানুষগুলো কেমন যেন যন্ত্রের মতো, কাজ, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির মোহের পিছনে ছুটে চলেছেন। পরিবর্তনের হাওয়ায় তার সাথে ভিন্ন সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার প্রবণায় আমাদের জীবন থেকে দিনকে দিন শ্রদ্ধাবোধ, মানবতাবোধ, সৌজন্যতাবোধ,মমত্ববোধ, অতিথিপরায়নতা বিশেষ করে বাঙ্গালিপনা হারিয়ে যাচ্ছে।
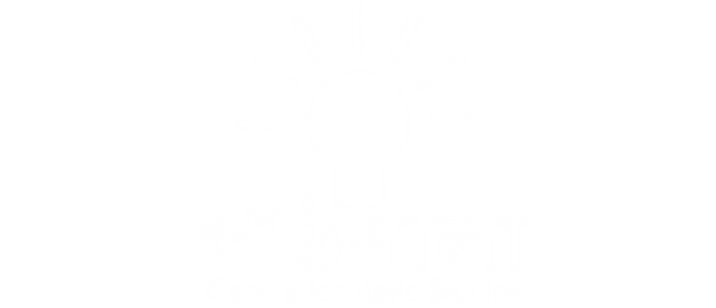
আপনার মন্তব্য লিখুন